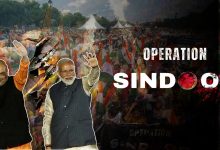রামকৃষ্ণ সংঘের সূচনাপর্ব, দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগর এবং আলমবাজার
The beginning of the Ramakrishna Sangha, from Dakshineswar to Baranagar and Alambazar

Truth Of Bengal: স্বামী বলভদ্রানন্দ: রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর পূর্তি হয়েছে গত ১ মে ২০২২ তারিখে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে স্বামীজী বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তের উপস্থিতিতে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ৫ মে ১৮৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, নবপ্রতিষ্ঠিত এই মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যধারা এবং কারা কারা থাকবেন এর পরিচালকমণ্ডলীতে।
‘রামকৃষ্ণ মিশন’ ছাড়াও আমরা ‘রামকৃষ্ণ মঠ’ কথাটিও শুনি। দু’টি মিলেই আমাদের ঠাকুর- মা-স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সংঘ। ভারতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মঠ একটি রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট এবং রামকৃষ্ণ মিশন একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দু’টি সংস্থা মিলে মিশে একাকার। কারণ, রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরাই রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সর্বক্ষণের সেক্রেটারি ও সহযোগী সন্ন্যাসী রূপে মনোনীত হন এবং রামকৃষ্ণ মঠ-এর সর্বোচ্চ পরিচালক মণ্ডলীতে (বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ-এ) যে কজন সন্ন্যাসী থাকেন, তাঁরাই থাকেন রামকৃষ্ণ মিশন-এর সর্বোচ্চ পরিচালক মণ্ডলী বা গভর্নিং বডিতেও।
অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, রামকৃষ্ণ সংঘ, বিশেষত ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামীজীর চিন্তা থেকে এসেছে এবং তিনিই এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যখন সব সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন জগজ্জননী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, এই অবতারে তাঁকে কী কী করতে হবে। তার মধ্যে একটি হল, তাঁর জীবনে তিনি যেসব উদার ধর্মভাব উপলব্ধি করেছেন, এমন একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায় তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে, যার মাধ্যমে সেই সব উদার ও মহৎ ভাবগুলো জগতে প্রচারিত হয়ে চলবে। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, যত মত তত পথ, সব ধর্মই মানুষকে সেই এক ভগবানের দিকেই নিয়ে যায়, মানুষকে ভগবান মনে করে সেবা অর্থাৎ শিবজ্ঞানে জীবসেবা-প্রভৃতি যে ভাবগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেই ভাবগুলি জাগ্রত থাকবে ঐ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে। এই ধর্মসম্প্রদায়ই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শরীর যাওয়ার আগে কাশীপুরে দিনের পর দিন নরেন্দ্রনাথকে আলাদা করে ডেকে ভবিষ্যতের ওই সঙ্ঘের কথা বলে গিয়েছিলেন। কোন ধরনের হবে সেই সঙ্ঘ, স্বামীজী এবং অন্য সন্ন্যাসী-গুরুভাইয়েরা কীভাবে চলবেন সেই সঙ্ঘকে বাস্তবায়িত করতে, এসব তিনি স্বামীজীকে বলে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র স্বামীজীকেই বলে গিয়েছিলেন এসব কথা, কারণ তিনি জানতেন এবং অন্য গুরুভাইয়েরাও বুঝতেন, স্বামীজীই তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের নেতা। কারণ তিনি শুধু প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যেই সেরা নন, ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তিতে এবং সবাইকে ভালবাসার শক্তিতেও তিনি সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
এই কাশীপুরেই ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে একজন (বুড়োগোপালদা, পরে সন্ন্যাস নিয়ে নাম হয়েছিল স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ঠাকুরকে একদিন বললেন, মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের জন্য কোলকাতায় অনেক সন্ন্যাসী এসেছেন, তাদের তিনি গেরুয়াবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দান করতে চান। ঠাকুর নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতিদের দেখিয়ে বললেন, এঁদের মতো সাধু কোথাও পাওয়া যাবে না। এঁদেরকে ওসব দিলেই তাঁর যথেষ্ট পূণ্য হবে। বুড়োগোপালদা সেই অনুযায়ী কয়েকটি গেরুয়াবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা এনে ঠাকুরকে দিলেন। তার মধ্যে থেকে ঠাকুর এগারোটি বস্ত্র ও মালা বেছে নিলেন এবং তখন তাঁর কাছে যেসব যুবক ভক্তরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে নিজে হাতে করে একটি গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা দিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একাদশ প্রেসিডেন্ট, পণ্ডিত ও উপলব্ধিমান সন্ন্যাসী স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁর ‘যুগনায়ক বিবেকানন্দ’ গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইহাই আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বলিতে পারা যায়।’
সেদিন ঠাকুরের কাছে যাঁরা গেরুয়া কাপড় পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন, নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, লাটু, কালী এবং বুড়োগোপাল নিজে। শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলজন সন্ন্যাসী-শিষ্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা হলেন, ভবিষ্যতের অখণ্ডানন্দজী, বিজ্ঞানানন্দজী, সুবোধানন্দজী, ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী। এই ঘটনাটি মকরসংক্রান্তির সময় হয়েছিল বলে এটিকে ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসের কোনও একদিনের ঘটনা বলে প্রথম থেকেই সকলের জানা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই তারিখটি নির্দিষ্টভাবে জানা গিয়েছে। তারিখটি ছিল ১২ জানুয়ারি ১৮৮৬। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুগাবতারের হাতে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট সঙ্ঘের স্থাপনা হয়েছে তাঁর প্রিয় শিষ্য, নয়নের মণি, ভাবী সঙ্ঘের রূপকার ও প্রধান স্তম্ভ বিবেকানন্দের জন্মদিবসে।
দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথকে নিজের কাছে ডেকে দরজা বন্ধ করে দুই তিন ঘণ্টা ধরে ভবিষ্যতে তাঁকে কী কী করতে হবে, সেই সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। তারপর মহাসমাধির যখন আর মাত্র তিন-চার দিন বাকি আছে, তখন তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে ডেকে তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলেন। নরেন্দ্রনাথ বাহ্যসংজ্ঞা হারালেন। বোধহয় সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন বাহ্যসংজ্ঞা ফিরল, তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন, ‘আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি।’ দেহত্যাগের যখন দু’দিন মাত্র বাকি, ঠাকুর আবার ডাকলেন নরেন্দ্রনাথকে। তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্যদের সামনেই ঠাকুর স্পষ্টভাবে নরেন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁদের দায়িত্ব নিতে। বললেন, ‘দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।’ এইভাবে স্পষ্টভাবে ঠাকুর সঙ্ঘ গড়ে দিয়ে গেলেন, সঙ্ঘনেতাকেও নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেলেন এবং তা তিনি করলেন সঙ্ঘনেতা ও তাঁর রত্ন-সদৃশ সহকারীদের সামনে।
শুধু তাই নয়। পিতার অবর্তমানে দায়িত্বশীল মাতাকেই তো একাধারে পিতা ও মাতা হয়ে উঠতে হয় পিতৃহীন সন্তানদের কাছে। দেহত্যাগের আগে শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য-সন্তানদেরও অগোচরে, তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবীকে সেই ভূমিকায় প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। সারদাদেবীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ছিল ‘গণ্ডিভাঙা মাতৃত্ব’ এবং ভগবতীর সাক্ষাৎ অবতাররূপে অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি।
শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে তাঁর অবর্তমানে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের কাছে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্ররূপে বিরাজ করেছেন, আবার মাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকেও ছাপিয়ে গিয়ে ওই ঘরছাড়া ত্যাগীদের জীবন সর্বদা স্নেহসিক্ত করে রেখেছেন তাঁদের সুখে-দুঃখে ও সংগ্রামে। নিরন্তর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন তাঁদের প্রতি এবং প্রার্থনা করে চলেছেন এই সঙ্ঘের জন্য। সেই জন্যেই স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে বলরাম মন্দিরে যে সভায় ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সভার সূচনাতেই মাকে ‘সঙ্ঘজননী’, ‘আদ্যাশক্তি’, ‘সঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্রী ও পালয়িত্রী’ রূপে ঘোষণা করে শুভ কাজের প্রারম্ভে যেন মঙ্গলাচরণ করেছিলেন।
ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ১৮৮৬-র অক্টোবর মাসে বরানগর মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। ত্যাগী শিষ্যরা এইবার একে একে ঘর ছেড়ে এখানে এসে বাস করতে শুরু করলেন। ত্যাগ-তপস্যা- শাস্ত্রপাঠ এবং অপরিসীম দারিদ্র্য ও কৃচ্ছতায় অতিবাহিত হয়ে চলে তাঁদের জীবন। জগন্মাতা যে সঙ্ঘের স্থাপনা করতে ঠাকুরকে নির্দেশ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের অন্তরগুলিকে একসূত্রে গেঁথে এবং তাঁদের অধিকাংশের হাতে গৈরিক বস্ত্র তুলে দিয়ে যে সঙ্ঘের প্রতীকী সূচনা নিজেই করে গেছিলেন, বরানগর মঠ সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম চোখে দেখতে পাওয়া বাস্তব রূপ।
১৮৮৬-র ডিসেম্বরে ত্যাগী-যুবকরা আঁটপুরে গেলেন প্রেমানন্দজী মহারাজের (তখন বাবুরাম) বাড়িতে। প্রতিদিন ধুনি জ্বালিয়ে শীতের খোলা আকাশের নীচে এই যুবকরা দীর্ঘ সময় ধ্যান ও সৎপ্রসঙ্গে কাটাতেন। দিন-তারিখ-বার-নক্ষত্রের হুঁশ থাকত না তাঁদের। এক রাতে ধ্যানের শেষে নেতা নরেন্দ্রনাথ উদ্দীপনাময় ভাষায় যিশুখ্রিস্টের অপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্যপূত জীবনের কথা বলে তাঁদের বৈরাগ্যকে আরও উদ্দীপিত করে দিলেন। ধুনির পবিত্র আগুনকে সাক্ষী রেখে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁরা যিশুখ্রিস্টের শিষ্যদের মতো পরিপূর্ণ ত্যাগের জীবন বেছে নিয়ে দেশে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার, পবিত্র, ঈশ্বরনির্ভর জীবনের বাণী ছড়িয়ে দেবেন।
পরে জানা গেল, সেটি ছিল ক্রিসমাস ইভের রাত, ২৪ ডিসেম্বর–যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্ব রজনী। তাঁদের মনে হল, শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সাধুরা যেমন বিরজাহোম করে সন্ন্যাসের সঙ্কল্প, গেরুয়া বস্ত্র ও সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেন— অবিলম্বে তাঁদের তা করা উচিত। এই অদ্ভুত সমাপতন (coincidence) যেন তাঁরই প্রতি ইঙ্গিত। বরানগর মঠে ফিরে এসেই তাঁরা বিরজাহোম করে শাস্ত্রসম্মতভাবে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন। তাঁদের নতুন নাম হল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, প্রভৃতি। স্বামীজী তখন ‘বিবিদিষানন্দ’ নামটি নিয়েছিলেন। ১৮৯১ সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি চিঠিপত্রে ‘বিবেকানন্দ’ নামটি লিখতে শুরু করেন। তখনও খেতড়ি রাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। কাজেই, অনেকে যে বলে থাকেন, খেতড়ির রাজা তাঁকে এই নাম দিয়েছিলেন, সেটি ভুল।
স্বামী গম্ভীরানন্দজীর ‘যুগনায়ক বিবেকানন্দ’ গ্রন্থ অনুযায়ী এই বরানগর মঠ-ই প্রথম ‘রামকৃষ্ণ মঠ’। এখানে মঠ ১৮৮৬-র অক্টোবর থেকে প্রায় পাঁচ বছর ছিল। রামকৃষ্ণ মঠ যখন বরানগরে প্রায় ৪ বছর ধরে স্থাপিত হয়েছে, তখনই (১৮৯০-এর জুলাইয়ে) স্বামীজী শেষবারের মতো পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে পড়েন। এটিই ছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনের দীর্ঘতম অধ্যায়। তাঁর জীবনের এই অংশটি ‘বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা’ নামে অভিহিত হয়। এরপরে তিনি শিকাগো থেকে শুরু করে সমগ্র আমেরিকায়, এবং ইংল্যান্ডেও, বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বিশ্বখ্যাত বিবেকানন্দ রূপে কোলকাতায় ফিরে এলেন ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।
পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামীজী যে মঠে এসে পদার্পণ করলেন তা বরানগর মঠ নয় আলমবাজার মঠ। স্বামীজী যখন ভারত-পরিক্রমায় রত, তখনই একসময় (১৮৯১-র নভেম্বর মাসে) মঠ বরানগর থেকে আলমবাজারে উঠে আসে। স্বামীজীর জীবনের এই ভারত-পরিক্রমা পর্বটি তাঁর ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ হয়ে ওঠার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগিনী নিবেদিতার মতে, বিবেকানন্দ গড়ে উঠেছেন তিনটি প্রভাব বা উপাদানের সমাহারে। সেই তিনটি মহান উপাদান হল, (১) ভারতের চিরন্তন শাস্ত্র, (২) তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং (৩) তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। শাস্ত্র পড়ে তিনি শাস্ত্রের চিরন্তন সত্যগুলির কথা জেনেছিলেন। কিন্তু সেগুলি যে আজও সত্য, তা বুঝেছিলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণর সংস্পর্শে এসে। নিবেদিতা তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন, ‘In his Master, Sri RamkrishnaParamhansa. Swami Vivekananda found that verification of the ancient texts which his heart and his reason demanded.’
স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় ও যুক্তিবোধ প্রাচীন শাস্ত্রের একটা প্রমাণ দেখতে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সেই প্রমাণ তিনি পেলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শুধু তাই নয়, ‘Here was the reality which the books only broken described.’ – শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি যে সত্যের সাক্ষাৎ পেলেন, শাস্ত্রের মধ্যে তার মাত্র আংশিক প্রকাশ। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আধ্যাত্মিকতার যে সামগ্রিক প্রকাশ ঘটেছে, তা শাস্ত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। In his Guru, RamkrishnaParamhansa, Vivekananda found the key to life’- জীবনরহস্যের চাবিকাঠিটি বিবেকানন্দ নিজের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই খুঁজে পেলেন।
স্বামীজীর গুরুভাইয়েরা দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগর মঠ পর্যন্ত পর্যায়ে যে স্বামীজীকে পেয়েছিলেন, ভালবেসেছিলেন, যাঁর ভালবাসা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রয়েছিলেন–সেই বিবেকানন্দ কিন্তু তখনও পর্যন্ত এতদূরই তৈরি হয়েছিলেন। সেই বিবেকানন্দও অতীব বিরাট। কিন্তু ভবিষ্যতে জগৎ যে বিবেকানন্দকে পেয়েছে, জগতের প্রয়োজন ছিল যে বিবেকানন্দের এবং অনাগত কাল ধরে যে বিবেকানন্দকে জগৎ স্মরণ ও অনুসরণ করে চলবে সেই বিবেকানন্দের নির্মাণ কিন্তু বরানগর মঠ পর্যন্ত পর্বে সম্পূর্ণ হয়নি। তখনও বাকি ছিল ভারত-পরিক্রমা পর্বটি।
নিবেদিতা স্পষ্ট করে সেই কথা লিখেছেন, “Even now, however, the preparation for his own task was not complete. He had yet to wander throughout the length and breadth of India, from the Himalaya to Cape Corner” — তখনও বিবেকানন্দের বাকি ছিল, যে কাজ করার জন্য তিনি এসেছিলেন, সেই কাজের জন্য ঠিক ঠিক প্রস্তুত হয়ে নেওয়ার। কারণ তখনও যে বাকি ছিল সমগ্র ভারতের মধ্য দিয়ে পরিব্রাজক রূপে বিচরণ করার এবং হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গোটা ভারতটিকে সচক্ষে দেখার, সর্ব প্রকার মানুষের সঙ্গে মিশে প্রকৃত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করবার। বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা আসলে ভারত-আবিষ্কার। তাঁর নিজের জন্য এবং ভারতবাসীর জন্যও। ভারতের শক্তি ও দুর্বলতা, গৌরব ও লজ্জা, সম্ভাবনা ও সমস্যা, এককথায় অতীত ও বর্তমান ভারতের সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি তিনি এইসময় স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করলেন এবং কীভাবে শুধু ইতিবাচক দিকগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি সর্বসুন্দর মহান ভারতকে রূপ দেওয়া যায় তার সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশও এই ভারত-পরিক্রমার কালে তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, যা তিনি পরবর্তীকালে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন।
(প্রথমপর্ব)