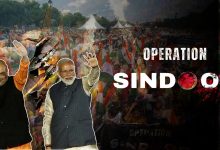‘আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই…’
"I will forever find myself in this Bengal..."

Truth Of Bengal: রুমনা সরকার: “আমরা বাঙালি, সবাই বাংলা মা’র সন্তান বাংলা ভূমির জল ও হাওয়ায় তৈরি মোদের প্রাণ।। মোদের দেহ, মোদের ভাষা, মোদের নাচ আর গান বাংলা-ভূমির মাটি হাওয়া জলেতে নির্মাণ।”
খুব ছোটবেলাও যখন ভৌগোলিক স্থান, সীমা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি, তখন ব্রতচারী ক্লাসে শেখা এই সুরারোপিত ছড়াটি অবচতনে এই বোধের সঞ্চয় করেছিল যে ‘আমরা বাঙালি’ আর ‘বাংলা মা’র সন্তান’। তারপর আস্তে আস্তে ধারণা জন্মাল পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে, জানলাম আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ- এখানে বাসস্থান বলেই আমরা বাঙালি আর বাংলা আমার মাতৃভাষা। এভাবেই আমার অনুভবে রবীন্দ্রনাথ এলেন, চেতনায় নজরুল। শিখলাম নতুন শব্দ এপার বাংলা, ওপার বাংলা। যদিও তার সারবত্তা খুব একটা বুঝে উঠতে পারিনি। ‘পূর্ব’ এবং ‘পশ্চিম’-এর সমীকরণ যে ততটাও সহজ নয়, তা আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও বুঝতে পালাম।
পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বাংলা নবজাগরণের ইতিহাস যখন পড়তে শুরু করলাম নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় কিংবা নারীশিক্ষার জনক বা বিধবা বিবাহের সূচনাকর্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এগুলি পড়তে পড়তেই এক অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করতাম বাঙালি হিসাবে। এর সাথেই নাড়া দিয়ে গেল ‘হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন’- সত্যিই তো বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা সাহিত্য বিবিধ মণিমাণিক্য পরিপূর্ণ। বাংলাতেই তো আমার আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম।
“বাংলা আমার জীবনানন্দ
বাংলা প্রাণের সুখ…”
এ তো গেল বাংলার নবজাগরণ আর বাংলার সংস্কার আন্দোলনের দোলায় দোলায়িত ‘আমি বাঙালি’। ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস এবং সেই আন্দোলনে বাঙালি বিপ্লবীদের সগর্ব অংশগ্রহণ বারে বারে আন্দোলিত করেছে আমার বাঙালি সত্তাকে, বাঙালি বীর বিপ্লবী ও শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস বাঙালি হিসবে একাত্ম করেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা অধ্যায়ের সঙ্গে। দেশনায়ক নেতাজী এই বাংলারই সন্তান- এ যেন সকল বাঙালির গর্বের অভিব্যক্তি। বাঙালির সাথে এক অকপট আত্মীয়তার সম্পর্ক নেতাজির। আবার স্বামী বিবেকানন্দ তিনিও আপামর বাঙালির স্বামীজি। Neo Hinduism-এর প্রবক্তা, বাঙালিকে দিশা দেখানোর পথ প্রদর্শক।
আচ্ছা এই সবটুকু ভালোত্ব আর ইতিবাচক দিকই কি কেবলমাত্র বাঙালিকে সূচিত করে? ভুলি কী করে?
“অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ীজীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে বসে।”
জটলা, আড্ডা এ তো বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য। Facebook কিংবা Whatsapp বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের বহু আগে থেকেই বাঙালির পাড়ার মোড়ের ‘চায়ের দোকান’ বিশ্ববিদ্যালয়ের রমরমা। রসেবশে বাঙালির অন্যতম নস্টালজিয়া তো কফিহাউস, বসন্ত কেবিন কিংবা
প্যারামাউন্ট, অবশ্য বলা ভালো তথাকথিত ‘intellectual’ বাঙালির নস্টালজিয়া। আসলে সামাজিক স্তরবিন্যাসের যেখানেই অবস্থিতি হোক না কেন, আমরা বাঙালিরা আড্ডাবাজ। PNPC করেন না এমন বাঙালি সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার, বাঙালির আড্ডায় গল্পের গরু গাছে উঠবে না এমনটা হয় না। বাঙালির আড্ডায় ঘটি-বাঙাল, ইলিশ-চিংড়ি-ফুটবল কিংবা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, রাজনীতি-অর্থনীতি-সিনেমা ক্রিকেট-গান সবই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উত্তর কলকাতার রকের আড্ডা তো সর্বজনবিদিত।
বিশ্বব্যাপী বাঙালির অনায়স পদচারণা, তবুও অধিকাংশ বাঙালি অনুভব করেন সোনার বাংলার প্রতি এক অদ্ভুত নাড়ীর টান। সত্যিই বাংলায় অনেক কিছুই নেই বিদেশের নিরিখে, অন্য উন্নত দেশ কিংবা রাজ্যের তুলনায় বাংলার অর্থ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, চাকরি কিংবা বিনিয়োগ বা ব্যবসার বাজার নেই তবু এই বাংলায় যা আছে, যে আবেগ, অনুভূতি, মানবতাবোধ তা একেবারেই অনন্য।
এসবই বাঙালি হিসাবে আমায় গর্বিত করে। আমি বাঙালি কারণ আমার দার্জিলিং আছে, আমার শান্তিনিকেতন আছে, আমার সুন্দরবন আছে। আছে আমার কলকাতা- নন্দন, একাডেমি, রবীদ্রসদন, ভিক্টোরিয়া; গড়ের মাঠ, প্রিন্সেপ ঘাট- এ তালিকা লিখতে বসলে দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। পাড়ার চায়ের দোকানের আড্ডা, সিঙাড়া, কচুরি-জিলিপির দোকানের লম্বা লাইন, ফুচকা, ঝালমুড়ি থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের দোকানের এগরোল, মোগলাই কিংবা dinner-এর চটজলদি সমাধান রুটি-তরকা, সবতেই আমার চেনা বাঙালিয়ানার ছক। দুর্গাপূজা আপামর বাঙালির মতো আমারও আবেগ। অধিকাংশ বাঙালিই দুর্গাপুজোর কটা দিন ঠাকুর দেখে, ঘুরে-বেড়িয়ে, খাওয়া-দাওয়ার সাথে জমিয়ে হুল্লোড় করেই কাটাতে চান। আমিও তো এর ব্যতিক্রম নই।
তবে হ্যাঁ, একবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কিন্তু কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী, বা বলা ভালো পরিবর্তনপন্থী। আদব-কায়দা, চাল-চলনে বেশ কিছুটা পশ্চিমের সভ্যতার অনুসরণকারী। হতে পারে তা বিশ্বায়ন বা Globalization-এর প্রভাব। যে ব্যাপারটা চিন্তার, তা হল অন্ধ
অনুকরণস্পৃহা। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রীতিনীতি সবেতেই গ্রহণ-বর্জন চলতেই থাকে কিন্তু তা যখন পশ্চিমানুসারী হয়ে ওঠে সেটা ‘বাংলাটা ঠিক আসে না’, উদ্বেগালনের মধ্যে দিয়েই কেবল বাঙালি সত্তার বড়াই করেন। দিনghbour-এর প্রতিশব্দ ‘প্রতিবেশীর থেকে পড়োসন’ শব্দটির Neighবহার করেন বা এই শব্দটিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। লেকিন, পরস্তু এসব শব্দের তো অনায়স যাতায়াত কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি- ‘This chair is so ছোট না, I was sitting হাঁটুমুড়ে’ ‘That day I ate বাঁধাকপি with কাঁটা’।
আসলে আমাকে যেভাবেই হোক ইংরেজি বলতে হবে- সে শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাই হোক না কেন! নইলে বন্ধুমহলে মান থাকে না যে! ইংরেজি বলাতে দোষের কিছু নেই। সমস্যা হল বাঙালি হিসেবে বাংলাকে উপেক্ষা করা। আগামী প্রজন্ম যাতে বাংলা ভাষার মাধুর্যকে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করতে পারে বাঙালি হিসাবে তার দায় অবশ্যই আমার, যাতে আগামী প্রজন্ম খুব সহজেই বলতে পারে- “আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি বাংলায় হাহাকার আমি সব দেখে শুনে ক্ষেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার।”
বাংলা আমার মাতৃভূমি, বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস, গৌরবময় মনীষা সবই আমার একান্ত আপন। সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা অপার সৌন্দর্যময় বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি তাই বাংলার নদী-মাঠ ধানক্ষেত ভালোবেসে এই বাংলাতেই পুনজন্মের যে স্বপ্নপ্ন কবি জীবনানন্দ বাঙালির হৃদয়ে প্রোথিত করে গেছেন আমিও তার ব্যতিক্রম নই।
মনে রাখতে হবে যে সময়ের প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী, বিশেষত নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, টরন্টো, প্যারিস, বাগুণি তার সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ দেশ ছাড়ছে, ছাড়ছে রাজ্যও। তবু কোথাও অনুভব করছে শিকড়ের টান। ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, বাজার অর্থনীতির বিস্তার এসবের কারণে বাঙালি দেশ ছাড়লেও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইয়ের শরিক অধিকাংশ বাঙালি। নিজেদের সংস্কৃতিকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ করে নিজেদের সংস্কৃতির মানোন্নয়নের চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদের পূর্বসূরীদের সূচিত পথ ধরেই ‘বাংলা’ ও ‘বাঙালি’র উত্তরাধিকারকে বহন করতে হবে।
সৌজন্যে- কণ্ঠস্বর