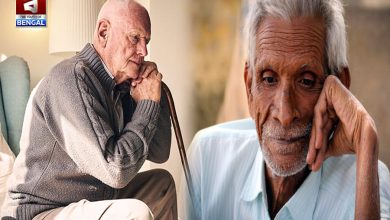কলকাতার নরেন বিশ্ব-বিবেকানন্দ হয়ে আজ শহরে ফিরেছিলেন
Kolkata's Naren Biswa-Vivekananda returned to the city today

Truth Of Bengal: স্বামী বলভদ্রানন্দ লেখক: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ ১২৮ বছর আগে আজকের এই দিনটিতেই কলকাতার নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ রূপে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তারিখটি ছিল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার যুবক নরেন্দ্রনাথ, ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানুষের কল্যাণে সমগ্র জগতে ছড়িয়ে দেবে এই যুবকই।
তাঁর অপর যে ১৫ জন সন্ন্যাসী শিষ্য তাঁরাও প্রত্যেকে ভবিষ্যতে বিরাট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হবেন, কিন্তু নরেন্দ্র সবার ওপরে। তাই চার বছর পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মহা নিশায় শ্রী রামকৃষ্ণ যখন দেহত্যাগ করলেন, নরেন্দ্রনাথকে তাঁর সমস্ত শক্তি অর্পণ করে গেলেন। তারও আগে নরেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁকে হতে হবে বিরাট বটগাছের মতো, যার ছায়ায় সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় নেবে।
শুধু নিজের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ নরেনের ব্রত হতে পারে না। তাঁর জীবন ব্যতীত হবে সকলের মুক্তির জন্য সকালের কল্যাণের জন্য। আর বলে গেলেন, একটি সন্ন্যাসী সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে, যে সন্ন্যাসী সংঘর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ বেঁচে থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ মানেই সনাতন ভারতের আদর্শ। সেই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার শুধু ভারতের প্রয়োজনেই নয়, সারা পৃথিবীর প্রয়োজনে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েক মাস পরেই (১৮৮৬ সালের ১৯ অক্টোবর) নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরানগর মঠ গড়ে উঠেছিল।
বরানগর মঠ থেকে মাঝে মাঝেই বিবেকানন্দ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী রূপে বেরিয়ে পড়তেন। কারণ ভারতীয় সন্ন্যাসীদের চিরকালের ধারাই হল পরিব্রাজক হয়ে ঘোরা। তিনি শেষবারের মতো পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে। ভারত পরিক্রমা করতে করতে ভারতের শক্তি দুর্বলতা, গৌরব ও লজ্জা– এক কথায় ভারতের সামগ্রিক ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে তিনি আবিষ্কার করলেন। তিনি আরও আবিষ্কার করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই ভারতের সনাতন শাস্ত্রের ঘণীভূত মূর্তি, আবার শ্রীরামকৃষ্ণই চিরন্তন ভারতবর্ষের ঘণীভূত রূপ।
ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, যখন বিবেকানন্দের কাছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতবর্ষ এবং ভারতের সনাতন ধর্ম একাকার রূপে প্রতিভাত হল, তখনই বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর সামনে দাঁড়ানোর জন্য উপযুক্ত হলেন। বিবেকানন্দের জীবনের এই অধ্যায়টি আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।
বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন ১৮৯৩ সালের ৩১ মে। শিকাগো পৌঁছেছিলেন ৩০ জুলাই ১৮৯৩। বিশ্বধর্ম মহাসভা চলেছিল ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ধর্মমহাসভার প্রথম দিনে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতেই তিনি গোটা আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। এরপরেও তিনি ধর্ম মহাসভার মূল শাখা এবং বিজ্ঞান শাখায় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯ সেপ্টেম্বরের হিন্দুধর্ম বক্তৃতা, ২০ সেপ্টেম্বরের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা যাতে তিনি বলেছিলেন ভারতে ধর্মের অভাব নেই অভাব রয়েছে অন্নের এবং ২৭ সেপ্টেম্বরের বিদায়ী ভাষণ।
তাঁর ভাষণ শুনে আমেরিকার মানুষ বলতে শুরু করলেন, আমরা এঁর দেশে ধর্ম প্রচারক পাঠাই? এঁদেরই উচিত আমাদের দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানো। ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিস্টার মারুইন মেরি স্নেল তাঁর সম্বন্ধে লিখলেন, ‘নিঃসন্দেহে তিনিই (বিবেকানন্দই) ছিলেন ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। খ্রিস্টান বা অ-খ্রিস্টান যে কোনও বক্তার চেয়ে শ্রোতারা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করত।
যেখানেই তিনি যেতেন লোক তাঁকে ঘিরে থাকত। আর তাঁর প্রত্যেকটি কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত । …আমেরিকা ভারতবর্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁকে পাঠানোর জন্য এবং ভারতবর্ষের কাছে আমেরিকার প্রার্থনা, তাঁর মতো এরকম মানুষ যেন সে আরও বেশি সংখ্যায় পাঠায়।’
কলকাতার মানুষ শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজির সাফল্যের কথা শিহরিত বিস্ময়ে সরাসরি শুনেছিলেন ধর্মমহাসভার অন্যতম বৌদ্ধ প্রতিনিধি অনাগরিক ধর্মপালের কাছ থেকে। তিনি ধর্ম মহাসভার পরই দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে একটি বক্তৃতায় স্বামীজি সম্বন্ধে বলেছিলেন, ‘আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ধর্মমহাসভায় মহান হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মতো আর কেউ সকলের মনোযোগ এমন করে আকর্ষণ করতে পারেননি। … যেখানেই তিনি যেতেন, মানুষ তাঁর চারপাশে ভিড় করে আসতো এবং যা-কিছু তিনি বলতেন তাই লোকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনত। আমি বলতে পারি তিনি সমগ্র দেশের জন্য বিরাট কাজ করেছেন এবং বাংলার গর্ববোধ করা উচিত এজন্য যে সেই বিরাট ধর্ম মহাসভায় তিনিই সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন।’
চার বছর ধরে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার করে স্বামীজি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। এরও বেশ কিছুদিন আগে স্বামীজি যখন রয়েছেন আমেরিকারই ডেট্রয়েট শহরে, তখন অন্তরঙ্গ পাশ্চাত্য শিষ্যদের কাছে স্বামীজি একদিন আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, ‘ভারতকে শুনতেই হবে আমার কথা। আমি ভারতের মূল ধরে নাড়িয়ে দেবো। আমি তার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইয়ে দেব! এ হল ভারত, আমার ভারত! আমি বুকের রক্ত তুলে যে বেদান্তকে এখানে মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দিয়ে গেলাম একমাত্র ভারতই পারবে ঠিক ঠিক তার কদর করতে। বিজয়োল্লাসে ভারত আমাকে বুকে তুলে নেবে।’
স্বামীজির এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি স্বামীজি কলম্বোয় পদার্পণ করেন এবং বর্তমান ভারত ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে দিনটি এখন স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস।
দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র দিগ্বিজয়ী বীরের মতো সম্মান পেতে পেতে স্বামীজি অগ্রসর হতে থাকেন চেন্নাই-এর দিকে। রামনাদ, পরমকুডি, মনমাদুরা, মাদুরা ও কুম্ভকর্ণ হয়ে স্বামীজি ট্রেন ধরেছিলেন চেন্নাইয়ের উদ্দেশে। মাঝখানে একটি ছোট স্টেশনে কয়েকশো লোক উপস্থিত হয়েছেন স্বামীজিকে দর্শন করবেন বলে। কিন্তু তাঁরা যখন শুনলেন ওই ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থামবে না, তখন তাঁরা সবাই রেললাইনে শুয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে স্বামীজির ট্রেনটিকে থেমে যেতে হল। স্বামীজি দরজার কাছে এসে তাদের দেখা দিলেন। তাঁরা তৃপ্ত হলেন এবং ট্রেন আবার ছুটে ছুটল চেন্নাইয়ের দিকে।
রেললাইনে যারা শুয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল সূরজ রাও। সে কিন্তু ফিরে গেল না। স্বামীজির ওই ক্ষণিক দর্শন তাকে পাগল করে দিয়েছে, আর সম্ভব নয় স্বামীজির কাছ থেকে দূরে থাকা। রেললাইন ধরে সেও এগিয়ে চলল চেন্নাই-এর দিকে। পথ সংক্ষেপ করার জন্য সমুদ্র তীর ধরে চলেছেন।
সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য! সমুদ্রের ধারে হতদরিদ্র জেলেদের যে সারি সারি কুঁড়েঘর রয়েছে, সেখানে সবাই যেন কী উৎসবে মেতে উঠেছে। তাদের ঘরে ঘরে আলোক মালা। শিশুরাও নাচ গান আনন্দ করছে। একদল শিশুকে সুরজ রাও জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাই, আজ তোমাদের কিসের উৎসব?’ শিশুরা জবাব দিল, ‘তুমি জানো না, আমাদের জগৎ গুরু এসে গেছেন।’ সুরাজ রাও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বুঝতে দেরি হলো না কে এই জগৎ গুরু। দরিদ্র জেলেদের শিশুরাও যাঁর আগমনে আনন্দমুখর। স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তন এই ভাবেই সেদিন সর্বশ্রেণির ভারতবাসীর প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করেছিল।
মাদ্রাজে স্বামীজি পৌঁছেছিলেন ৬ জানুয়ারি ১৮৯৭। ছিলেন ৯টি দিন। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, এই ৯টি দিন সমগ্র মাদ্রাজ নগরী যেন তাদের প্রিয় মহোৎসব ‘নবরাত্রির’ মতোই মেতে উঠেছিল স্বামীজিকে ঘিরে। এবং স্বামীজিও মাদ্রাজকে উপলক্ষ করে দেশ জাতি ব্যক্তি ও সমষ্টি ‘জাগানিয়া’ চিরন্তন বাণীসমূহ বিতরণ করে চললেন সর্বত্র– যে বাণীগুলির অমোঘ প্রভাব সম্বন্ধে রোমা রোলা বলেছেন, ‘যীশুখ্রিস্টের আহ্বানে মৃত লেজারাস যেমন জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে এসেছিল, স্বামীজির আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষও তেমনই কুম্ভকর্ণের মহানিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠেছিল। চেন্নাই স্বামীজিকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র লিখেছিল, ‘সুপ্রাচীনকাল থেকে মাদ্রাজে কেউ কখনও ভারতীয় বা ইউরোপীয় কাউকেই এরকম ভাবে সংবর্ধনা জানাতে দেখেনি।’
মাদ্রাজ থেকে স্বামীজি জাহাজে করে কলকাতা রওনা হলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭-এর সকালে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রিবেলা জাহাজ এসে বজবজ বন্দরে নোঙর করল। স্বামীজি সেদিন সে রাতটা জাহাজেই কাটালেন। পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় তিনি বজবজ বন্দরে পদার্পণ করলেন। স্বামীজির জন্য কলকাতার বিশিষ্টজনেরা যে অভ্যর্থনা সমিতি তৈরি করেছিল, তাদের অনুরোধে পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্বামীজির জন্য একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিল। সেই ট্রেনে চড়ে স্বামীজি সকাল সাড়ে সাতটায় শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছন।
তখন সেখানে লোক থিক থিক করছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, ওই শীতের সকালেও সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে কুড়ি হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছনোর মুখে যখন হুইসেল দিল তখনই সমবেত জনসাধারণ আবেগে আত্মহারা হয়ে বিরাট কলরব করে উঠল। ট্রেন থামলে স্বামীজি প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করলেন। তখন কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্বামীজিকে প্রণাম করলেন, যাঁরা দূরে ছিলেন তাঁরা সমবেতভাবে জয়ধ্বনি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের।
ভিড়ের মধ্যে অনেক কষ্ট করে স্বামীজিকে বের করে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া হল। স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন সেভিয়ার দম্পতি যাঁরা স্বামীজির কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন। স্বামীজির গাড়ি ছাড়ার আগেই একদল ছাত্র স্বামীজির ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলিকে খুলে দিয়ে নিজেরাই স্বামীজির গাড়ি টানতে টানতে নিয়ে চলল রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের) দিকে। পেছনে অনুসরণ করে চলল এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা, যাতে রয়েছে কীর্তনের দল, অগণিত মানুষ এবং সারিসারি ঘোড়ার গাড়ি। পথের বিভিন্ন স্থানে সুসজ্জিত তোরণে লেখা ছিল, ‘জয় স্বামীজী, জয় রামকৃষ্ণ এবং স্বাগত।
স্বামী রিপন কলেজে পৌঁছলে সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হলো। সবকিছু দেখে স্বামীজি নিজেই অভিভূত হয়ে যান। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি দুই একটি ধন্যবাদ সূচক কথাবার্তা বললেন মাত্র। এরপরই স্বামীজিকে নিয়ে যাওয়া হয় বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে, সেখানেই স্বামীজি এবং তাঁর অতিথিদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
এখানে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং গৃহীগুরু ভাইয়ের। তারা হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে তার নিজের মানসপুত্র বলতেন সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সামনে দেখেই স্বামীজির মনে পড়ে গেল যেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন। বয়সে তাঁর থেকে ৯দিনের বড় হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজি তাঁকে প্রণাম করে সংস্কৃতে বললেন: ‘গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু’–গুরুর পুত্র গুরুর মতোই প্রণম্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামীজির এই অভূতপূর্ব কীর্তির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাই দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজিকে প্রণাম করে বললেন, ‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতাসম’।
সন্ধ্যেবেলায় তিনি চলে এলেন আলমবাজার মঠে, সব গুরু ভাইদের মধ্যে। এই দিনই তাঁর প্রথম আলমবাজার মঠে পদার্পণ। স্বামীজি কলকাতায় প্রথম ভাষণটি দিয়েছিলেন ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ তারিখে শোভাবাজার রাজবাড়িতে। সীমিত জায়গার জন্য ফ্রি পাশ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবুও কয়েক সহস্র লোক হয়েছিল। স্বামীজি বলেছিলেন, ‘কলকাতাবাসী যুবকগন… ওঠো, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এক মহাবলি প্রার্থনা করছে। … আমি এক সময় অতি নগণ্য বালক মাত্র ছিলাম। আমি একসময় এই কলকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলে বেড়াতাম। যদি আমি এত দূর করে থাকি তবে তোমরা আমার চেয়েও কত বেশি কাজ করতে পারো… ভেবো না তোমরা দরিদ্র, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন। কে কোথায় দেখেছে টাকায় মানুষ করেছে? মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে।’
স্বামীজির কলকাতায় প্রত্যাবর্তন স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তনের একটি অংশ। দেশে ফেরার পর ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকার সম্পাদককে স্বামীজি ভারতীয় চরিত্রের প্রধান ত্রুটি কী সেটি নির্দেশ করে বলেছিলেন, ‘দেশশুদ্ধ লোক নিজেদের সোনাটাকে রাংতা বলে মনে করছে, আর পাশ্চাত্যের রাংতাটাকে সোনা বলে মনে করছে।’ স্বামীজি ভারতবাসীকে শিখিয়েছেন, নিজেদের সোনাটিকে সোনা বলেই চিনে নিয়ে আত্মবিশ্বাসে ও আত্মশ্রদ্ধায় ঋজু হয়ে দাঁড়াতে। তাই বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন বা কলকাতা প্রত্যাবর্তন কোনও সফল মানুষের নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন নয়।
এ হল ভারত-আত্মার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন। সুপমণ্ডিত রাজনীতিবিদ চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারি (মাদ্রাজের এক সময়কার মুখ্যমন্ত্রী ও নেহরু মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) যথার্থই বলেছেন, ‘আমাদের সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কতটা ঋণী। ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলন করে দিয়েছেন। আমরা অন্ধ ছিলাম তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতাও লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সবকিছু জন্যই তাই আমরা বিবেকানন্দের কাছে ঋণী।’