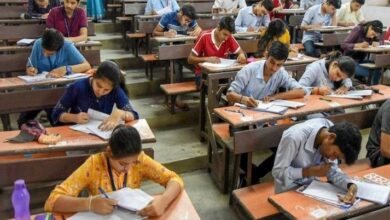Bangla Jago Desk: কাজল ব্যানার্জী: শৈশব, বাল্য, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য– প্রত্যেক মানুষের জীবনের অবশ্যম্ভাবী ক্রমপর্যায়। জীবনের এই কালচক্রে কৈশোর কালের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশি বলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা। যে কোনেও ব্যক্তিই তার জন্মস্থান, শৈশবকাল ও বাল্যকালের স্মৃতি কিছুটা হলেও বিস্মৃত হতেই পারেন। যৌবনের আনন্দও সাময়িক।
আর বার্ধক্য এক গতানুগতিক প্রতীক্ষাময় সময়। কিন্তু কৈশোর-কালকে বিস্মৃত হওয়া কখনেও-ই সম্ভব নয়। জন্মভূমি বা কর্মভূমির থেকেও জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে কৈশোরের স্মৃতি। শৈশব পেরিয়ে বাল্য থেকে ব্যক্তিজীবনে প্রবেশের এই সন্ধিক্ষণই ব্যক্তির জীবনের গতি প্রকৃতির নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক।
আর জীবনের এই কৈশোরকালের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে হাইস্কুলের স্মৃতি। জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে তাই কৈশোর কাটানো হাইস্কুল, হাইস্কুলের বন্ধু-বান্ধব ও হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা থেকেই যায়। ফলত, হাইস্কুলের প্রতি একটু অন্যরকম আবেগ ও অনুভূতির ঐতিহ্যকে বহন করেই কেটে যায় জীবনের পরবর্তী বছরগুলি।
অতীতে স্কুল বলতে আমাদের মনে যে ছবিটা আজও ভেসে ওঠে তা হল, আমাদের কৈশোর কাটানো সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়। কিন্তু বর্তমানে সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি তৈরি হয়েছে অসংখ্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিযোগিতার বাজারে সন্তানকে অন্যদের থেকে এগিয়ে দিতে অভিভাবকদেরও আগ্রহও সেই বেসরকারি স্কুলগুলির দিকেই।
এবং তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির প্রবণতা কমছে! কয়েকটি বিদ্যালয়ে আসনের থেকেও উদ্বৃত্ত শিক্ষার্থী থাকলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ই কিন্তু ধুঁকছে ছাত্রাল্পতায়! এই ট্ট্যাডিশন চলতে থাকলে কিন্তু অনেক সরকার পোষিত বিদ্যালয়ই উঠে যাবে অচিরে। তাই সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলগুলিকে বাঁচাতেই হবে। কারণ গরিব মানুষের পক্ষে সরকারি স্কুলের বিকল্পে পৌঁছনোর কোনেও রাস্তাই নেই।
কিন্তু সরকারি স্কুলগুলিকে ব্যবহার করার লোকের অভাব না থাকলেও সেগুলির স্বার্থরক্ষার্থে কাজ করেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি। এমনকী ২০-২৫ বছর আগেও স্কুলগুলির অবস্থা এমন ছিল না। সরকারি বিধি-নিষেধ, বিভিন্ন আইন-কানুন, আদালতের নির্দেশ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রচার-মাধ্যমের চাপ, নিত্যনতুন প্রযুক্তির হাতছানি ইত্যাদি নানাবিধ কারনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রচুর বিবর্তন এসেছে বর্তমান সময়ে।
বর্তমান সময়ে সরকারি শিক্ষাঙ্গনের গুরুত্বহানির একটা অন্যতম বড় কারণ ভ্রান্ত শিক্ষানীতি ও গুরুকূলকে লঘুকরণের প্রয়াস। বর্তমানে সমাজে শিক্ষকের সম্মান ও গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান। এর পক্ষে বা বিপক্ষে অনেকে অনেক কিছুই বলতেই পারেন। কিন্তু একটা বড় কারণ হল– ক্রমবর্ধমান শিক্ষার হার! আমরা যে যুগের শিক্ষকের সম্মানের কথা বলে থাকি, সেই যুগে শিক্ষিত মানুষ সংখ্যায় খুব কম ছিলেন! তখন, সমাজে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়।
তার মধ্যে আবার শিক্ষকের সংখ্যা ছিল আরেও কম। নারীশিক্ষা ছিল চরম অবহেলিত! ফলে শিক্ষিকার সংখ্যাও ছিল খুবই কম! স্পষ্টতই সমাজে শিক্ষকের সঙ্কট ছিল! শিক্ষিত ব্যক্তি তথা শিক্ষকের ওপর সমাজের সকলকেই কমবেশি নির্ভর করতে হতো।পাড়ায় একজন মাস্টারমশাই থাকলে তাঁর কোনেও বিকল্প পাওয়া যেত না। অনেকটা বর্তমান সময়ের ডাক্তারদের মতো।কাগজ ত্র, চিঠিপত্র ইত্যাদি সকল বিষয়ে শিক্ষকেরই শরণাপন্ন হতে হতো।ফলে শিক্ষকতা সমাজে সম্মানজনক পদে পরিণত হয়েছিল। আর তৎকালীন সময়ে, সামাজিক সম্মান বা খ্যাতির আকর্ষণেও অনেকেই শিক্ষকতার স্বপ্ন দেখতেন।
কিন্তু শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মাস্টারমশাইদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। নারীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দিদিমনিও পাওয়া গেল। এই প্রাচুর্যের সঙ্গেই শিক্ষকতার গুরুত্বহানির সূচনা! এজি গার্ডিনার তাঁর ‘অন লেটার রাইটিং’প্রবন্ধে লিখেছেন ‘’কোনও বস্তুর সহজ প্রাপ্যতা সেটির গুরুত্ব হানি ঘটায়।‘’ ঠিক, একই ভাবে সমাজে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকতার পদমর্যাদা হ্রাসের জন্য অনেকখানিই দায়ী।
ধরুন, আমাদের রাজ্যের প্রত্যেক পাড়ায় যদি জনা-দশেক করে এমডি ডাক্তার থাকতেন, তা হলে কি ডাক্তারবাবুরাও বর্তমানে যেটুকু সম্মান পান, সেইটুকু পেতেন? এরসঙ্গে আছে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মসংস্থানের অভাব। ফলে শিক্ষিত ব্যক্তির ‘জীবনের লক্ষ্য’ বর্তমানে মূল্যহীন। কারণ, বেঁচে থাকার জন্য সে একটা কাজ চায়। সেখানে তার পছন্দ-অপছন্দ অর্থহীন।
হাতে বিকল্প কাজের সুযোগ না থাকায় শিক্ষকতা পেলে সেটিই তাঁর পেশায় পরিণত হতে বাধ্য। ফলে মন থেকে মেনে নিতে না পারা সত্ত্বেও অনেকেরই পেশা শিক্ষকতা। তাই এই পেশায় ভুলভ্রান্তি বা প্রেষণার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই। সেই সুযোগ থেকেই বিরূপ সমালোচনা। আর বিরূপ সমালোচনা থেকেও ঘটতে থাকে সামগ্রিক-শিক্ষকতার গুরুত্বহানি।
এছাড়া রয়েছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কনসেপ্ট, টিভি, মোবাইল, স্মার্টফোন, ভিডিয়ো গেম, পারিবারিক অসঙ্গতি ও স্কুল-আওয়ারে কোচিং-এর মতো কিছু মারণ রোগ যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্যতম অন্তরায়। বাহ্যিক বিষয়ের হাতছানি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি তৈরিতে প্রতিবন্ধতা তৈরি করছে। শিক্ষকতা জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতায় আমায় উপলব্ধি হল, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিক্ষণ কর্মসূচি হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে আবেগমূলক মিথোস্ক্রিয়া।
একটি অবশ্যই দ্বি-পাক্ষিক কর্মসূচি।শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করলেই শ্রেণি-শিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের এবং সম্ভব হলে তাদের অভিভাবকদেরও পৃথক অভিমুখীকরণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা দরকার।
শ্রেণি-শিক্ষণের বিষয়টিকে একজন সঙ্গীতশিল্পীর শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শ্রোতৃমণ্ডলী ভালে না হয়ে বিশৃঙ্খলা-পরায়ণ হলে শিল্পীর পক্ষে ভাল সঙ্গীত পরিবেশন কোনেওমতেই সম্ভব নয়। শ্রোতারা শিল্পীর পরিবেশনায় আন্তরিক ভাবে অংশ নিলে, তারিফ করলে, করতালি দিলে শিল্পীর কন্ঠ থেকে ক্রমান্বয়ে আরও ভাল সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায়। ক্রমশ শিল্পীর শিল্প-প্রতিভার পূর্ণ-প্রকাশ ঘটতে থাকে। কিন্তু বিশৃঙ্খলার মধ্যে কখনেও-ই শিল্পীর পক্ষে ভালে পরিবেশনা সম্ভব নয়, উপরন্তু তার শিল্পীসত্তারও চরম ক্ষতির সম্ভাবনা।
একইভাবে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা-পরায়ণ হয়ে শ্রেণি-শিক্ষণে মনোযোগী হলে শিক্ষক বা শিক্ষিকার শিক্ষণের গুণগত মান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শ্রেণিকক্ষে যদি প্রতিদিন সালিশি সভা বা বিচার সভা করতে হয়, স্কুল পালানো শিক্ষার্থীর সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে হয়, তা হলে শ্রেণি-শিক্ষণটা হবে কখন? বর্তমান সামাজিক পেক্ষাপটে, প্রাইভেট টিউশন নির্ভরতার যুগে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এখন যন্ত্রণাময়। যে সব শিক্ষক বা শিক্ষিকা অনুভূতি-প্রবণ বা ক্লাসে পড়াতে চেষ্টা করেন, বাড়িতে টিউশন করেন না, তাঁদের পক্ষে বছরের পর বছর ক্লাসে এভাবে পড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা শুধু গ্লানিময়ই নয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষিকার অপূরণীয় মানসিক ক্ষতিও বটে।
আসলে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আবেগ ও অনুভূতির সম্পর্ককে মেরে ফেলেছে নিয়মের নানা বেড়াজাল। তাই, স্কুল শিক্ষকদের বর্তমানে সবার আগে মাথায় রাখতে হয় নিজের পিঠ বাঁচানোর কথা। তাই, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমানে দেখনদারিই বেশি।
বর্তমানে স্কুল শিক্ষকগণ আট-পিরিয়ড পর্যন্ত করাচ্ছেন কিনা, তাঁরা ৪.৩৫ মিনিট পর্যন্ত থাকছেন কিনা– এসব নিয়েই সমাজের বেশি মাথাব্যথা। স্বাভাবিক কারণেই, বিদ্যালয় পরিচালকগণ সেই শর্তগুলিই পূরণ করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে চান। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত পাঠদানের সুযোগ আছে কি না বা কী করলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ঠিকমত পাঠ দিতে পারেন– তা দেখার কেউ নাই!
আদর্শ শিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থী-মাফিক শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার। দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষায় উচ্চ-মেধাবীদের জন্য পৃথক ও উচ্চ-গুণগতমানের শিক্ষণ আবশ্যক। কিন্তু কোনেও সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সংবিধান অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার। তাই কোনেও সরকারের পক্ষে শিক্ষার্থীদের আলাদা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে সত্যিকারের শিক্ষণ দিতে হলে, শিক্ষার্থীর আয়ত্ত করার ক্ষমতা অনুযায়ীই শিক্ষণ দিতে হয়।
তাই সরকারি প্রতিষ্ঠানে সবাইকে এক ছাদের তলায় একসঙ্গে শিক্ষণ দিতে হলে গড় প্রক্রিয়া অবলম্বণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ফলে উন্নত মেধাবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার নিম্নমেধার শিক্ষার্থী সেই স্তর পর্যন্তও অনুধাবন করতে পারে না। ফলে বর্তমান স্কুল শিক্ষায় উভয়ের কেউই তেমন কোনও উপকৃত হয় না। তাই বলে স্কুলে আসার ফলে শিক্ষার্থীদের কোনেও উপকার হয় না এমনটি বলছি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুলে যেটা হয়, তা হল– স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার স্পিরিট তৈরি করে। স্কুলে আসার ফলে তাঁরা সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। তাঁদের মধ্যে আত্মসক্রিয়তা জাগ্রত হয়। আর খুব সত্যি কথা হল, অধিকাংশ স্কুলেই এখন তেমনভাবে শ্রেণি-শিক্ষণগত লেখাপড়া হয় না।
বর্তমান পরিস্থিতি ও পূর্বের পরিস্থিতির মধ্যে বিশাল ফারাক তৈরি হয়ে গিয়েছে।বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণিতে মেধা যাচাই করে সরকার পোষিত কোনেও স্কুলেই আর ভর্তি নেওয়া যায় না। ফলে সূচনায় শিক্ষার্থীদের মেধা অনুযায়ী স্ক্রিনিং করার সুযোগ নেই। আবার ফেল ব্যবস্থা না থাকায় পাশ না করে কিছু না শিখে ওপরের শ্রেণিতে উঠে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে নবম শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থীই ইংরেজিতে নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে পারে না। সেই শিক্ষার্থী গণিতে সূচক বা লগারিদম শিখবে কীভাবে?
সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি-শিক্ষণ দিতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের শিক্ষণ-সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষণের ব্যবস্থা ও তাদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ। কিন্তু আগেই বলেছি, সরকারের পক্ষে শিক্ষার্থীদের আলাদা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই স্ক্রিনিংটা সম্ভব। ফলে সেখানে সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার সুযোগ তৈরি করাই যায়। তাই, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সমস্যার সমাধান দুরূহ বুঝে নিজেদের সন্তানদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে বাধ্য হই আমরা অনেকেই।
সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের অকারণ পরীক্ষায় বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকদের খুশি করতে সময়ও ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। ফলে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় তারা সময় সংকুলান করতে পারছে না। সরকারি স্কুলে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের নম্বর পাইয়ে দেওয়ার পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। বেসরকারি স্কুলে এইসকল বিষয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কম।
সেখানে ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা ও পরিকাঠামোও অনেক বেশি উন্নত। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের গুণগত মান এখনেও পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। তা ছাড়া আমাদের মতো নিম্নবিত্ত-প্রধান রাজ্যে বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করার সামর্থই বা ক’জনের আছে? তাই প্রতিবছ শুধু শিক্ষক দিবস উদযাপনের আনন্দে আপ্লুত হলেই শুধু চলবে না, সেইসঙ্গে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গণের সার্বিক স্বার্থরক্ষার জন্য নিস্বার্থভাবে পুনঃপুনঃ ভাবনারও প্রয়োজন।