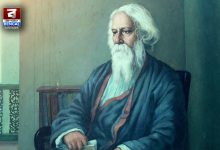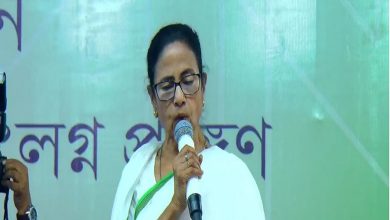বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ: বাঙালির এক গৌরবময় প্রতিষ্ঠান
Bengali Literary Council: A Glorious Institution of Bengalis

রাজু পারাল: তিলোত্তমা কলকাতার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে কত না গর্ব ও অহঙ্কার করার মতো জিনিস। আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো মানিকতলাতেও আছে পুস্তকে পরিপূর্ণ এক সংগ্রহালয়। পরিসরে অত বড় না হলেও খুব ছোট নয়। সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটে অবস্থিত ‘সাহিত্য পরিষদ’ প্রতিষ্ঠানটির কথা আজ প্রায় লোকের মুখে মুখে। কেন তৈরি হল ‘সাহিত্য পরিষদ’? বলা যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর মুল লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার।
জাতীয় শক্তিকে দৃঢ়ভাবে স্থাপনের জন্য শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত বলে মনে করতেন পরিষদের সদস্যরা। এক্ষেত্রে ঠাকুর বাড়ির উদ্যোগ এবং রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। মাতৃভাষার প্রসার ও উন্নতিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এল লিওটার্ড নামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী এক ফরাসি ভদ্রলোক এবং আর এক বঙ্গসন্তান ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর উদ্যোগে ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই কলকাতার শোভাবাজারে রাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাসভবনে স্থাপিত হয় ‘বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার’।
সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম সভাপতি ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ দেব, সহ সভাপতি ছিলেন লিওটার্ড ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। তবে বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরে যে মানুষটির নাম চিরজীবনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে তিনি হলেন কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়। তিনি সাহিত্য পরিষদের জন্য কলকাতার হালশীবাগানে আপার সার্কুলার রোডের ওপর জমি দান করেন।
যার ওপর নির্মিত হয় আজকের ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’। আর পরিষদের দোতলা তৈরির পুরো অর্থ দিয়েছিলেন লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়। পরে মণীন্দ্রচন্দ্র এই ভবনের পেছনে আরও জমি দেন, যেখানে পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয় ‘রমেশ ভবন’। প্রথমদিকে ‘বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারে’র মুখপত্র, সভার বিবরণ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলেও সাহিত্য পরিষদ গঠিত হওয়ার পরে এব্যাপারে কোনও কোনও সদস্যদের আপত্তি উঠলে উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবানুসারে অ্যাকাডেমির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়
‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’। পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদ বিষয়ের উপস্থাপনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলিতে আমরা কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, বাঙ্গালা দেশবাসী দশ জন লোক একত্র হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।’
১৩১৫ সালের ২১ অগ্রহায়ণ সাহিত্য পরিষদের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সূচনাপর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু নানাভাবে এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ আবেগদীপ্ত ভাষণে বলেন, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেকদিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবর্তীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে– তাহার এক নিত্য প্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালির চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালি চিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে। দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে।’ রবীন্দ্রনাথ যখন এই ভাষণ দেন তখনও তিনি বিশ্বকবি হননি। আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই ভাষণে সব বাঙালির মনের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।
সময়ে সময়ে বহু মনীষী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। যাঁর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি প্রথম ভারতীয় আইসিএস ) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্ব ব্যতিরেকে আর যাঁরা পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সারদাচরণ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখ।
বলা যায় বাঙালি মনীষীদের একটা বড় অংশই কোনও না কোনও ভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন নিরন্তর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একসময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘বাঙালির ইতিহাস নেই, সে আত্মবিস্মৃত জাতি।’ কথাটা নিষ্ঠুর শোনালেও একটা সময় পর্যন্ত তা ছিল বাস্তব সত্য। উনিশ শতকের একেবারে শেষ প্রান্তে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত হল, তার বহুমুখী কর্মচর্চার মাধ্যমে তৈরি হল আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের এক যৌথ প্রচেষ্টা। একথা অনস্বীকার্য বাংলা ও বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থান নিঃসন্দেহে অনেক উঁচুতে।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান অহঙ্কার হল এখানকার গ্রন্থাগারটি। পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি বড় গ্রন্থাগার স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, ‘পরিষদে দিন দিন শিক্ষিত লেখকগণের সমাগম হইতেছে এবং পরিষদ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশ যেরূপ শক্তি বিস্তার করিতেছে তাহাতে পরিষদের একটি পুস্তকালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক।’ গ্রন্থাকার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় তাঁরা যেন নিজেদের লিখিত বই গ্রন্থাগারে উপহার দেন।
রবীন্দ্রনাথ ‘কবি কাহিনী’ ,’বনফুল’, ‘বাল্মীকি প্রতিভা’, ‘কাল মৃগয়া’ , ‘সন্ধ্যা সঙ্গীত’ ইত্যাদি বেশ কিছু বই পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োদশ বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ৭৩টি প্রাচীন বই ও পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি থেকে পরিষদকে উপহার দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনেকেই তাঁদের পরিবারিক পুস্তক সংগ্রহ এখানে দান করেছেন। পরিষদের নিজস্ব সঞ্চয়, উপহার প্রাপ্ত ও দানলব্ধ সংগ্রহ ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রেমসুন্দর বসুর মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদ গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত হওয়ায় আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠাগার কেবল এ বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের একটা সেরা সংগ্রহালয়ে পরিণত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদস্থল।
বাংলা, সংস্কৃত, ওড়িয়া, ফার্সি, অসমীয়া ও তিব্বতি মিলিয়ে এখানে সংগ্রিহিত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের মতো। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গৌরপদ তরঙ্গিণী, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, শ্রী শ্রী পদকল্পতরু ইত্যাদি প্রাচীন পুঁথির মুদ্রণ ও প্রকাশিত হয়েছে এখান থেকে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংকলিত ‘শব্দকোষ’ এই সাহিত্য পরিষদ থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি ‘ভারতকোষের’ কয়েকটি খণ্ড এবং সাহিত্যসাধক চরিতমালার গ্রন্থাবলিগুলি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ গ্রন্থগুলি আজও বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত।
বাংলা ভাষা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন ভাষার বই এবং পত্রপত্রিকা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ আকর্ষণ তো বটেই, পাশাপাশি এখানকার চিত্রশালাও অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে যুগ যুগান্ত ধরে। দর্শকরা এখানেই দেখতে পাবেন রাজা রামমোহন রায়ের ব্যবহৃত পাগড়ি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত টেবিল, হস্তাক্ষর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, প্রখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর সম্বলিত বিভিন্ন চিঠি ও খ্যাতনামা বঙ্গ সন্তানদের ব্যবহৃত পোশাক, দোয়াত, কলম, চশমা, ঘড়ি, লাঠি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, কাঙাল হরিনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বিখ্যাত বঙ্গ সন্তানদের লেখা পাণ্ডুলিপিও এখানে দেখা যাবে। অনেক প্রাচীন দলিলও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এসব ছাড়া নানা দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তির সংগ্রহ এখানকার সংগ্রহশালার বিশেষ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়।
এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের ব্যাপারে একসময় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষদের সঙ্গে তাঁর স্বল্পকালীন যোগাযোগের সময়েই প্রাচীন মুদ্রা, বাংলার পাল ও সেনযুগের পাথরের মূর্তি, ভাস্কর্য, মন্দির, টেরাকোটার গুরুপ্তপূর্ণ সংগ্রহটি গড়ে ওঠে। পরিষদে অজস্র তৈলচিত্র ও বাঙালি মনীষীদের অসংখ্য ভাস্কর্য ও দেখা যায়। এছাড়া লোকশিল্পের নমুনা (লৌকিক দেবদেবী, পুতুল ও খেলনা, কাঠ ও শোলার কাজ, ডোকরা ও অন্যান্য ধাতু-ভাস্কর্য, পটচিত্র, চিত্রিত সরা, দশাবতার তাস, দুর্গমূর্তি ও চালচিত্র, বৃষকাষ্ঠ…) জেলা অনুযায়ী বিষয় ধরে সাজানো রয়েছে। এখানে সংগৃহীত রয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্য কাদম্বরী দেবীর হাতে বোনা ‘সাধের আসন’।
সর্বোপরি, যে পত্রিকার নাম উল্লেখ না করলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌরব বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয় তা হল এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ‘সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা’। বহু বছর ধরে চলা এই পত্রিকা আজও সাহিত্যের সেরা পত্রিকা হিসাবে গণ্য করা হয়। পরিশেষে একথা বলাই যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থিত উত্তর কলকাতার এই হেরিটেজ ভবনটি আগামী অনেক বছর বাংলা ও বাঙালিকে সঠিক পথ দেখাবে।