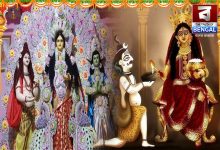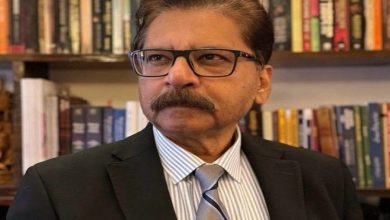শিয়ালদহ না হাওড়া-কোন পথে চলেছিল প্রথম ট্রেন জানেন?
Sealdah or Howrah - do you know which direction the first train was running

Truth of Bengal,কাজল ব্যানার্জিঃ ইংল্যান্ডের প্রথম রেলব্যবস্থার প্রচলন হয় ১৮২৫ সালে। সেখানে স্টকটন এবং ডার্লিংটনের মধ্যে প্রথম রেলগাড়ি চলে। এর পর সেদেশে পরবর্তী ৪০ বছরে ১৫ হাজার মাইল রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হয়। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জর্জ স্টিফেনসন এই কাজের মূল স্থপতি ছিলেন। ১৮২৫ সালে ইংল্যান্ডের স্টকটন এবং ডার্লিংটনের মধ্যে যে রেলপথ তৈরী হয় সেটিকেই বিশ্বেরও প্রথম রেলপথ বলা চলে কারণ এর আগে অন্য কোনো দেশে রেল ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। এর ঠিক পাঁচ বছরের মাথায়, ইংল্যান্ডেই প্রথম চালু হয় আন্তঃশহর বা ইন্টারসিটি রেলওয়ে। ১৮৩০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টারের মধ্যে রেল চলাচল শুরু হয়।
ভারতে রেল ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরেই। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি ভারতে রেলপথ চালু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৮৪৮থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল পদে ছিলেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে তাকেই ভারতীয় রেলের জনক বলা যেতে পারে। ভারতে রেলপথ প্রচলনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানিকে। এই কাজে মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বার্কলে সাহেব।
ভারতে রেলপথ স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের মূললক্ষ্য ছিল ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রীকে সহজে এবং সুলভে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পরিবহন করা যাতে মুনাফা বৃদ্ধি করা যায়। তবে সেইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসন পরিচালনা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দমনে দ্রুত সেনা পাঠানো, নীলের ব্যবসা ও সেইসঙ্গে রেলে যাত্রী পরিবহনের ব্যবসা সবই ছিল ইংরাজদের মাথায়। তবে এটাই ঠিক যে ব্রিটিশদের কারণেই ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। রাজতন্ত্র বা জমিদার তন্ত্র চালু থাকলে এদেশ যে প্রযুক্তির ব্যবহারে আরও পিছিয়ে পড়তো তা বলাই বাহুল্য।
ভারতে প্রথম রেললাইনটি ১৮৫৩ সালে বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) এবং থানের মধ্যে চালু হয়েছিল। ১৬ এপ্রিল ১৮৫৩ সালে, প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটি বোরি বন্দর (বোম্বাই) থেকে থানে পর্যন্ত ৩৪কিলোমিটারের দূরত্বে ১৪ টি কোচ এবং ৪০০যাত্রী নিয়ে যাত্রা করেছিল। সূচনা লগ্নে বেজে উঠেছিল ব্যান্ড ও বিউগল, সঙ্গে ২১টি তোপধ্বনি। সাক্ষী ছিলেন শত শত মানুষ। মোট ১৪ টি কামরায় সওয়ার হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন শহরের বহু গণ্যমান্য মানুষজন।
বাস্পচালিত সেই প্রথম ইঞ্জিনটির নাম ছিল এফ -১/৭৩৪। বেলা ঠিক দুটোয় যাত্রা শুরু করে ৩৪ কিমি পথ অতিক্রম করে সায়ন স্টেশনে জল নেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সেটি থানে স্টেশনে পৌঁছায় বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে। পরদিন (১৭ এপ্রিল) সেই যাত্রীদের নিয়ে আবার বোরি বন্দর স্টেশনে ফিরে আসে। তারও পরের দিন, অর্থাৎ সোমবার, ১৮ এপ্রিল, স্যর জামশেদজি জিজিবয় গোটা ট্রেনটি তাঁর পরিবারের জন্য ভাড়া নেন এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বে থেকে ওই ট্রেনে চেপে থানে যান, আবার সে দিনই বিকেলে ফিরে আসেন।
আমাদের রাজ্য বাংলায় প্রথম রেললাইনটি ১৫ আগস্ট, ১৮৫৪ সালে উদ্বোধন করা হয়েছিল। এটি হাওড়াকে হুগলির মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিল, যার দূরত্ব ছিল ২৪ মাইল (৩৯ কিমি)। এটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির (ইআইআর) একটি অংশ যেটি ব্রিটিশরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, ভারতের প্রাচীনতম এবং ব্যস্ততম স্টেশন গুলির মধ্যে একটি।
১৮৫৪ সালে এই স্টেশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বাংলায় রেল যোগাযোগের জন্য প্রধান গেটওয়ে হয়ে ওঠে এবং এটি একটি কেন্দ্রীয় হাব হিসাবে আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। হাওড়া-হুগলি লাইন দ্রুত বাংলার অন্যান্য অংশে প্রসারিত হয়। ১৮৫৫ সালের মধ্যে, লাইনটি বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৫৭ সালে, রানিগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয় খনি থেকে উত্তোলিত কয়লা পরিবহনের লক্ষ নিয়ে। তবে এটি কেবল কয়লা পরিবহনের সুবিধাই করেনি বরং বাংলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিকেও সংযুক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।
এরপর পাটশিল্পকে চাঙ্গা করার লক্ষমাত্রা নিয়ে ১৮৫৭ সালে, কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত একটি নতুন রেললাইন নির্মানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৫৭ সালে তৈরি হয় কলকাতা, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। বছর খানেকের মধ্যে তা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের অন্তর্ভুক্ত হয়। কলকাতা-ঢাকা রেলপথ নির্মানের দায়িত্ব বর্তান ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েরই উপর। শিয়ালদহে তখনও স্টেশন তৈরী হয়নি কিন্তু শিয়ালদহ-রানাঘাট রেলপথ পাতা শুরু হয়ে যায় সেই সময় থেকেই। ১৮৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত বাষ্প ইঞ্জিন ব্যবহার করে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের ট্রেন প্রথমবার ছুটতে শুরু করে।
এরপর ওয়াল্টার গ্র্যান ভিলের নকশা, পরিকল্পনায় ১৮৬৯-সালে শিয়ালদহ স্টেশনটি সম্পূর্ণ হয়। তার আগেই অবশ্য রানাঘাট পর্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত ছিল। স্বাধীনতার আগে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার সব ট্রেনই পূর্ববঙ্গের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করত। ১৮৭৮-এ চালু হয় দার্জিলিং মেল। সেই সময় শিয়ালদহ-রানাঘাট রেলপথই ছিল উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পথ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ট্রেনের জানালার ধারে বসে এই পথ দিয়েই পূর্ববঙ্গে যেতেন।
শিমুরালি, চাকদহ রেলস্টেশনগুলি ১৮৬২ সালে নির্মিত হয়। কিন্তু তখন কল্যাণী শহর তৈরী হয় নি। সেইসময় অধুনা কল্যাণী শহরের নাম ছিল রুজভেল্ট নগর। এখন যেখানে কল্যাণী স্টেশন সেখানে ছিল জঙ্গল। রেলপথ পাতার সময় এই জঙ্গল কাটা হয়। ১৮৮৩ সালে তৎকালীন সেই রুজভেল্ট নগরে চাঁদমারি হল্ট নামে রেলওয়ে স্টেশনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৩ সালে এটির নাম পরিবর্তন করে কল্যাণী করা হয়। ৭ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে, ট্র্যাকটি কল্যাণী প্রধান থেকে কল্যাণী সীমান্ত স্টেশন পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল।
ফলে রেলপথের বয়স এক হলেও শিমুরালি, চাকদহ ও রানাঘাট স্টেশনগুলি কল্যাণী রেল স্টেশনের থেকে কিছুটা প্রাচীন। এরপর কেটে গেছে অনেক বছর। স্টীম ইঞ্জিন থেকে ডিজেল ইঞ্জিন এবং ডিজেল থেকে বিদ্যুতচালিত ইঞ্জিনে বিবর্তন ঘটেছে। রেলের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে ধাপে ধাপে। শিয়ালদহ-রানাঘাট অংশের বিদ্যুতায়ন ১৯৬৩-৬৪ সালে। রানাঘাট-গেদে সেকশনটি ১৯৯৭-৯৮ সালে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়। তারপরে শিয়ালদহ এবং গেদে-এর মধ্যে ইএমইউ (ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। উল্লেখ্য রেলের সূচনালগ্নে পালপাড়ায় রেলপথ থাকলেও রেল স্টেশনটি ছিল না। পরবর্তী সময়ে মানুষের চাহিদাকে মান্যতা দিয়ে পালপাড়ায় ষ্টেশন চালু করা হয়।
স্টীম ইঞ্জিনের যুগে প্রতিটি ট্রেন চলার সময় ইঞ্জিনে একজন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকতেন শুধু চুল্লীতে কয়লা দেওয়া কাজে। সেই কয়লা রেললাইনে ফেলে দিয়ে চোরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকার নেওয়ার রেওয়াজও চালু ছিল। আমাদের শৈশব বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হয়ে গেলেও ইলেকট্রিক ও ডিজেল ইঞ্জিনের পাশাপাশি কিছু স্টীম-ইঞ্জিনও চলতো। ফলে আমরা শৈশবে ট্রেন থেকে কয়লা ফেলার ঘটনা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। রেলের কয়লা কালোপথে কম পয়সায় কিনে বহু ব্যবসায়ীকে ফুলেফেঁপে লাল হয়ে যেতেও দেখেছি। তথ্যসূত্রঃ নব্বইয়ের দশকের কিছু প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার বই, সংবাদপত্র ও উইকিপিডিয়া।