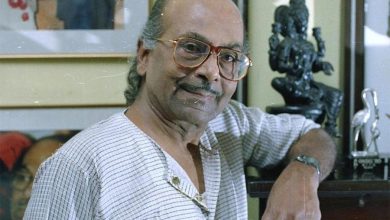ঈশ্বরচন্দ্রের অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু
Rajnarayan Bose took forward the unfinished work of Ishwar Chandra
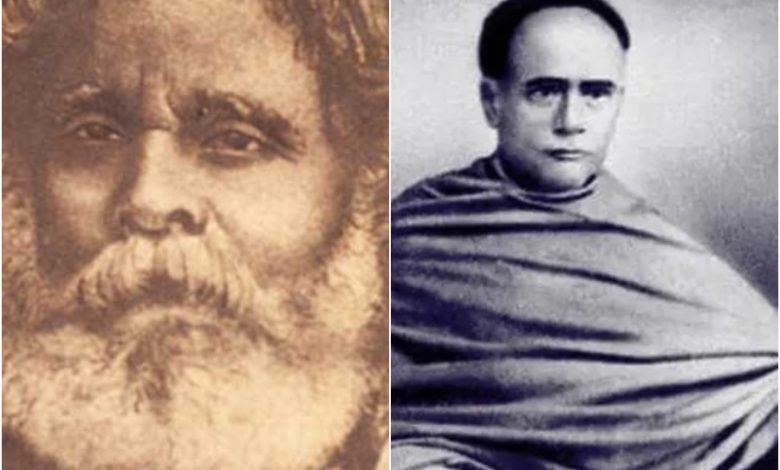
Truth Of Bengal: মধুবন চক্রবর্তী: জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু একজন যথার্থ সাহিত্য সমালোচক যেরকম ছিলেন, ছিলেন সমাজ সংস্কারক। সেরকম দুর্গম পথের সাধকও তাকে বলা যেতে পারে। বিশেষ করে বিধবাবিবাহ প্রথাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এই সমাজ সংস্কারক, বহু প্রতিবন্ধকতা ও অপমানকে অতিক্রম করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগেও বিধবাবিবাহের প্রচলনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যে প্রয়াসের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিরলস অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার কোন তুলনাই ছিল না। তাঁর হৃদয় কেঁদেছিল সেকালের সমগ্র হিন্দুর নারীর সমাজের দুর্গতি দুর্দশায়।
ঠিক সেরকমভাবেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজের সঙ্গে ছিল হৃদয়ের যোগ রাজনারায়ণ বসুর। পরবর্তী ক্ষেত্রে তার প্রচলিত সেই প্রথাকে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু। সেকালের সমগ্র হিন্দু নারীদের প্রতি তাঁরও ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান।
১৮৫৬ সালের আইনটি কেবলমাত্র বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের স্বীকৃতি দেয়নি, আইনটি যেমন বিবাহকে আইনসিদ্ধ করে। তেমনই মৃত স্বামীর এবং দ্বিতীয় বিবাহের এবং পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিতে অধিকারাদি সুনির্দিষ্ট করে। আইন বিধিবদ্ধ করার আগে এবং পরে বিধবাবিবাহ প্রচলন করার প্রচেষ্টার জন্য বিদ্যাসাগরকে নিদারুন এক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন অসীম সাহসী ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন, সফল করার ক্ষেত্রে সাহস প্রয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন একসময়ে কলকাতায় রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল।
আর সেই প্রবাহ রাজনারায়ণ বসুর জন্মভূমি মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল গোড়া হিন্দু সমাজ। উত্তাল হয়ে উঠেছিল গ্রামের মাতব্বররা। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে বাস্তবতাকে তুলে ধরেছিলেন, সেই মুক্তচিন্তা রাজনারায়ণ বসুর হৃদয় ছুঁয়েছিল। এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি যে বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় দীক্ষিত রাজনারায়ণ বসু সেই সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গ্রাম বোড়ালেও।
বিধবাবিবাহ আইনে পরিণত হলে, প্রথম বিবাহ করলেন কলকাতার শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৫৬ এর ডিসেম্বর মাসে। এরপর দ্বিতীয় বিবাহটি করলেন পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ। তৃতীয় চতুর্থ বিবাহ দানের কৃতিত্ব রাজনারায়ণ বসুর। আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসুর ‘আত্মচরিত’ অনুযায়ী দুটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।
যে দুটি করেন তাঁর সহোদর মদনমোহন বসু ও জেঠুতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু। প্রথম বিবাহ দুটি হিন্দু সমাজের হলেও পরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত হতে থাকে বিধবা বিবাহ আইনকে তাঁরা হাতিয়ার করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকারেরা জানিয়েছেন, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে মোট সাতটি বিধবাকন্যার বিবাহ হয়েছিল আর এইসব বিয়ের অধিকাংশের ব্যয় ভার বহন করেছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র।
বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হলেও, সবকটি বিবাহই যে সমাজ সংস্কারের মনোভাব নিয়ে ঘটেছিল তা কিন্তু নয়। বহু ক্ষেত্রেই অর্থের লোভে অথবা অন্য প্রলোভনে এই বিবাহ করা হয়। তার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের মনেও কম তিক্ততার জন্ম হয়নি। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর এই কঠিন সংগ্রামের পাশে পেয়েছিলেন একাধিক সমাজ সংস্কারককে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু।
তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সংস্কার তৈরি করতে হয় বাড়িতে থেকেই অর্থাৎ অন্দরমহল থেকেই সেই সংস্কার আন্দোলনের কাছ থেকে তিনি শুরু করেছিলেন। যদিও এর জন্য তাকে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। পরিবারের চোখে তাকে অনেক নিচু হতে হয়েছে। অপমানিত হতে হয়েছে। তার কাকা এবং মা সকলেই খুব অসুন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই কর্মকাণ্ডে।
সবাই তাকে দোষারোপ করেছিলেন কাকা বলেছিলেন তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম”.. গ্রামেও সেই একই চিত্র দেখা গিয়েছিল। গ্রামের মানুষ রীতিমতো হুমকি দিয়েছিল রাজনারায়ণ বসুকে। তারা বলেছিলেন রাজনারায়ণ বসুর গ্রামে আইলে আমরা ইট মারিব।
তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন,
” তাহা হইলে আমরা খুশি হইবো..
আমি বাঙালিকে উদাসীন জাত বলিয়া জানি”।
মেদিনীপুরে শুরু হয়ে গিয়েছিল চরম বিরোধিতা যার ফলে অনেকটাই উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু। একাধারে সংসারী মানুষ হলেও অন্যদিকে প্রতিবাদী কন্ঠস্বর তিনি কোনোও দিন রোধ করেননি ভয় পেয়ে, হূমকি হুঁশিয়ারির কাছে কোনদিন মাথা নত করেননি। পিছিয়ে যাননি তাঁর সংকল্প থেকে। যা ভেবেছেন তাই করে দেখিয়েছেন আর এখানেই তার মহত্ব।
এক সময়ের সরকারি উকিল হরনারায়ন দত্ত রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপাতে শুরু করেছিলেন।। ঘুরিয়ে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গোটা বিষয়টিতেই বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। বিভ্রান্ত করতে পারেনি সেই সময়ের পরিস্থিতি। কারণ তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ। সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনা করতেন। জানতেন আজকের এই আন্দোলনের জোয়ার ভবিষ্যতে একদিন সুনামিতে রূপান্তরিত হবে। বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সবসময়ই পাশে পেয়েছিলেন তিনি এই দুর্দশাগ্রস্ত দিনগুলিতে।
শুধুমাত্র বিধবা বিবাহের মতো সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের পাশে থাকাই নয় একসময় মদ্যপানের তীব্র বিরোধিতা ও করেছিলেন। ১৮৬০ সালে তৈরি করেছিলেন নতুন একটি সভা যা বাংলার বুকে এক নিদর্শন তৈরি করেছিল। সেই সভার নাম ছিল” সুরাপান নির্বাচননী সভা”। মদ্যপানের কুপ্রভাব নিয়ে প্রচার করা হত সেই সব থেকে। মদ্যপানের বিরোধিতা করে এক সময় বহু গানও রচনা করেছিলেন রাজনারায়ণ।
সভার পক্ষ থেকেও নানান গান রচনা করা হয়েছিল সেইসময়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে কোন সম্পন্ন আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি পরিবারে কোনও বালকের যেভাবে শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত ঠিক সেভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন রাজনারায়ণ। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর একাগ্রতা ও ভালোবাসা যতটা। ছিল, দখল যতটা ছিল।
বিজ্ঞান বা গণিতের প্রতি সেই পক্ষপাত অবশ্য ততটা ছিল না। যে তথ্য পাওয়া যায় তাঁরই উচ্চারিত একটি বাক্য থেকে। হেয়ার স্কুলের হেয়ার সাহেবের প্রবর্তিত বিতর্ক সভায় একবার তিনি whether science is preferable to literature এই প্রস্তাবের পক্ষে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন। লিখেছিলেন তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা দিয়েছি।
মাত্র ২৪ বছর বয়সে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন। প্রথম জীবনে কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের অধীনে অধ্যাপনা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে এসে তার রূপান্তর ঘটে, লিখেছিলেন আত্মচরিত। দেশবাসীকে জাতীয় মন্ত্রে একতাবদ্ধ করে স্বদেশের উন্নতি সাধনে হয়েছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মৌলিক দিকগুলো যাতে বিকশিত হয় সেদিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন।
পুরুষের সঙ্গে সমানতালে যাতে নারীরাও সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দিয়েছিলেন তিনি। আসলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল নারী জাতের কল্যাণের প্রচেষ্টা। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার। সেই আন্দোলনে ১৮৫৬র পরে বিধবাবিবাহ আইনকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো চেষ্টা করা হয়। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘আত্মচরিতে’ বেশ কয়েকটি বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়।
যেমন জানা যায় প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন ঢাকায় ব্রজসুন্দর মিত্র। তিনি কন্যাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন। এবং শিক্ষিত করার পর তাদের( বিধবা কন্যা সহ) ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। তবে হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজে কোনও বিধবা বিবাহই কিন্তু একেবারে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। অথবা সুসম্পন্ন হলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে নানান রকম জটিলতা বা গোলযোগের সৃষ্টি হয়।
রাজনারায়ণ বসুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে সব রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়েও তিনি তার এই সুদূরপ্রসারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিধবা বিবাহ প্রথাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ বা একজন সাহিত্যসমালোচক নয়, এক দুর্গম পথের সাধক বলা যায় তাকে।
সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের ধারক ও বাহক রাজনারায়ণ বসু বাঙলা বাঙালির গর্ব। অহংকার। ঈশ্বরচন্দ্রের অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহ প্রথাকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা রাজনারায়ণ বসু। সময়ের বিবর্তনে সমাজ সংস্কারক এই মানুষটিকে এই প্রজন্ম যাতে ভুলে না যায় এই কারণেই তুলে ধরা লেখাটি।