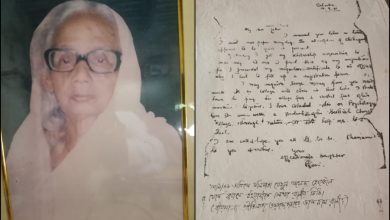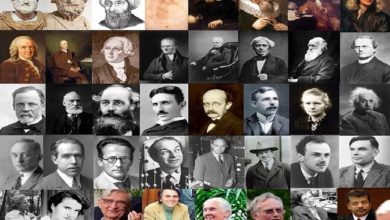মধুবন চক্রবর্তী: সময় বদলেছে। বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা চলাফেরার আদব-কায়দা। বদলেছে সিনেমার বিষয়। আন্তর্জাতিক সিনেমায় ঘটে গেছে বিপ্লব। নতুন থিম, নতুন কনসেপ্ট কন্টেন্ট নিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ছবি। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এখন শক্তিশালী। বিকল্প মাধ্যম বাড়ছে, বাড়ছে নতুনত্ব।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দাপটে এখন অনেকটাই কোণঠাসা প্রেক্ষাগৃহগুলি। তার মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু প্রেক্ষাগৃহে রমরমা ব্যবসা করছে। বেশ কিছু হিন্দি সিনেমা তামিল, তেলেগু, দক্ষিণী মালায়ালাম ছবিগুলির হিন্দি ভার্সন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের বিবর্তন ঘটলেও, বদলে যায় না ইতিহাসের দলিল। পথের নানা বাঁক, সে পথের পথিক আমরা। পথিকের পথের পাঁচালীর খবর এই প্রজন্ম রাখে কিনা জানি না। তবে যতই প্রযুক্তির দাপট আসুক না কেন, সৃষ্টি আর উচ্চতর আর্টের কাছে আমরা সবাই মাথা নত করি।
বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর এক জীবন্ত রূপরেখা তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। যা ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। সামাজিক ও মানবিক জীবনের কঠিন বাস্তবকে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। জীবনের এক করুন পাণ্ডুলিপি নির্মাণ করেছিলেন সামাজিক জীবনের জ্বলন্ত প্রেক্ষাপটে।
আটের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত প্রযুক্তির নানান পরিবর্তন ঘটেছে ক্যামেরার ক্ষেত্রে। পরিবর্তন এসেছে নানান লেন্সে। পরিবর্তন এসেছে তার গঠন, প্রয়োগ, ব্যবহারে। ফ্রেম পাল্টেছে চলচ্চিত্রের। ফ্রেম তো একটা দর্পণ। দর্পণ শুধুমাত্র দেখার বিষয় তো নয়, বিশেষ ভাবনারও প্রকাশ।
সত্যজিৎ রায় এমনই একজন চলচ্চিত্রকার ছিলেন যিনি ফ্রেম একে একে কাহিনির বিস্তার বোঝাতেন। তাঁর টাইপোগ্রাফি, তাঁর চিত্র ভাবনা, তার উপস্থাপনা সবটাই তাঁর। পাশাপাশি তার অঙ্কন দক্ষতা নিয়ে তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পারিপার্শ্বকে দেখা স্মৃতিতে তা ধরে রাখা তার উপযুক্ত প্রকাশ ঘটানো এবং পাশাপাশি দৃশ্যগুলিকে পরপর সাজিয়ে ফ্রেমে বন্দি করা, এক চরম সাধনার প্রকাশ। যা আগেও বলেছি, এক উচ্চতর ভাবনা বা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল পথের পাঁচালীকে। পথের পাঁচালীর স্ক্রিপ্ট মূলত দৃশ্য নির্ভর। যখন তিনি নিজেই ক্যামেরা চালাতে শুরু করেছিলেন তখন সবটাই নিজের হাতে করে নিতেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃশ্যগুলি ধরে ধরে ফ্রেমবন্দি করতেন। ক্যামেরাই হয়ে উঠেছিল তার শিল্পের তুলি তার সমস্ত দেখাটাই প্রেমের মধ্যে দিয়েই একটা চরিত্র পেতে শুরু করেছিল। এর সঙ্গে একটা বিরাট অংশ জড়িয়ে ছিল। সেটি হল সংগীত।
পথের পাঁচালীর সঙ্গীত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধুর্য্য, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। অপু ত্রয়ী চলচ্চিত্র ধারাবাহিকের প্রথম চলচ্চিত্র, পথের পাঁচালী, যেখানে সঙ্গীতের ব্যবহার এক ম্যাজিক্যাল চিত্রকল্প তৈরি করে। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা পথের পাঁচালীর মাধ্যমেই উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পায়। দেশজ সঙ্গীতের ভাব রূপ, ঘনত্ব শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অপার সৌন্দর্যকে প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, পথের পাঁচালীর সঙ্গীতের আবহ। শুধুমাত্র সিনেমা জন্য নয়, এ যেন ঘূর্ণায়মান জীবনের অনন্ত যাত্রার সুর। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই সিনেমার মিউজিক। বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের জীবনধারাকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে ব্যবহার করেছিলেন হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র সেতার। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশেষ কিছু রাগকে ব্যবহার করেছিলেন এই আবহসঙ্গীত তৈরির ক্ষেত্রে। চলচ্চিত্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাবহৃত হয়েছিল সেতারের ব্যঞ্জনা।
সেতারবাদকের সুর ধরে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হেঁটে চলেছে এক কিশোরী আর তার ভাই। ১৯৬২ সাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল Imorovization on the theam Music from pather pachali সেখানে মঞ্চে উঠে এসেছিলেন দু’জন শিল্পী। তবলায় কানাই দত্ত আর সঙ্গে এলেন আরও একজন প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুটের স্বাস্থ্যবান শরীরটা। মঞ্চে এসে বসলেন। হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের সেতার। আঙুলের মূর্ছনায় ছলকে উঠেছিল সমস্ত ব্যথা ও দুঃখ। দর্শক সেই সময় অনুভব করতে পেরেছিলেন, পথের পাঁচালীর অন্তরাত্মাকে।
একজন নবাগত পরিচালকের ছবিতে এই সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন, স্বয়ং সেতার বাদক। সত্যজিৎ রায় যখন পথের পাঁচালী নির্মাণ করেছেন, তখন আন্তর্জাতিকতার বিষয়টি তাঁর মাথায় ছিল। ছবির জগতে আসার অনেক আগে থেকেই রবিশঙ্করের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। রবিশঙ্কর তখন তরুণ। সত্যজিৎও তাই। দু’জনেই নবাগত। মুম্বইতে যে বার প্রথম দেখা হয়েছিল দু’জনের আলোচনা হয়েছিল ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে। ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে আলাদা ভাবে তেমন কোনও আগ্রহ না থাকলেও, মূলত পাশ্চাত্য সঙ্গীতেই আগ্রহ ছিল সত্যজিৎ রায়ের। রবিশঙ্কর এবং সত্যজিতের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল সেবার সঙ্গীত। সঙ্গীত বিষয়ক যে গভীর জ্ঞান ছিল সত্যজিতের, তা ভালভাবে বুঝে গিয়েছিলেন রবিশঙ্কর।
তাঁর স্মৃতিতে লিখছেন, ‘সেই সময় সতীদের বাড়িতে প্রথম দেখি সত্যজিৎকে, লম্বা ছিপ ছিপে যাকে বলে লাজুক তরুণ, প্রথম দর্শনে খুব ভাল লেগেছিল ওকে।’ এবং রবিশঙ্করের স্মৃতিতে আর একবার শোনা যায় তিনি বলছেন, এরপর পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে যখনই কলকাতায় গিয়েছি, এখানে ওখানে দেখা হতো ওর সঙ্গে। আমার তখন বেশ নাম হয়েছে সেতার শিল্পী হিসেবে। বেশ জনপ্রিয়তা। সাধারণত উঠতাম গিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। সত্যজিৎ তখন ডিজে কিমার বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করছেন। ওই পাড়া দিয়ে যেতে আসতে দেখতাম কলকাতায় আসা যাওয়ার ফাঁকেই জানতে পেরেছিলাম যে সত্যজিতের গভীর জ্ঞান ও আগ্রহ আছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বিষয়ে। ধীরে ধীরে রবিশঙ্করের সঙ্গে সত্যজিতের এক বন্ধুত্ব তৈরি হয়। ইতিমধ্যেই সত্যজিৎ রায় অফিসের কাজে বিদেশ যাচ্ছেন এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র দেখছেন যার মধ্যে রয়েছে বাইসাইকেল থিভস।
পথের পাঁচালীর প্রায় বছর দশেক আগেই সিনেমা সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন রবিশঙ্কর। তবে বাংলায় নয় বোম্বাইয়ে হিন্দি ছবিতে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল চেতন আনন্দের। নিচানগর ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। আরও বেশ কিছু হিন্দি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছেন। কবি মাহমুদ ইকবালের ‘সারে জাহা সে আচ্ছা তে…’ সুর দিলেন। সেই গান গাইলেন প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পরে এই গানটি লতা মঙ্গেশকর যখন গেয়েছিলেন, তখন সেই গানের সুরে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে যা গ্রাফি পুরস্কারে ভূষিত হয়। রবিশঙ্করের এই কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে সত্যজিৎকে ভাবাতে শুরু করে। সত্যজিৎ এবং রবিশঙ্করের মধ্যে এক পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। পথের পাঁচালী সঙ্গীত পরিচালনার কথা রবিশঙ্করকে যখন তিনি বলেছিলেন, এক কথায় রাজি হয়েছিলেন রবিশঙ্কর।
পথের পাঁচালীকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সত্যজিতের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। পণ্ডিত রবিশঙ্কর তখন ভারতীয় সঙ্গীতকে এক আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আর তাই সত্যজিৎ রায় সরাসরি পথের পাঁচালী ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে রবি শঙ্করকেই বেছে নিয়েছিলেন। পরিকল্পনা এবং নির্মাণ করেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। রবিশঙ্করের স্মৃতি থেকে পাওয়া যায়… ‘পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতেই উঠি আমি কলকাতায় এলে। বেশ মনে আছে একদিন দুপুরে সত্যজিৎ সেখানে হাজির। ততদিনে আমি জেনেছিলাম উনি একটা নতুন ধরনের বাংলা ছবি তুলছেন। বিভূতি বাবুর পথের পাঁচালী বই নিয়ে ছবি। সেদিন দুপুরে উনি নিজের ছবির বিষয়ে একটু বলেন, তাতে সুর করার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন…’ সত্যজিৎ রায় সেদিন যেটা জানিয়েছিলেন তিনি খুব কষ্টেই এই ছবিটা করছেন এবং রবিশঙ্কর তাতে যদি সুর দেন তা হলে সত্যি ভাল হয় এবং সেদিন রাস দেখানোর ব্যবস্থা করার কথাও বলেছিলেন।
পরের দিন টালিগঞ্জের ভবানী সিনেমাতে রাস দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই রাত থেকে রবি শঙ্কর একেবারে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। মন থেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়কে এবং সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই ছবির সুর তিনিই করবেন। ‘রাস দেখতে দেখতে ছবির থিম মিউজিকটা যেন গুনগুন করে ভেতর ভেতর পাক দিয়ে উঠছিল’ জানাচ্ছেন রবিশঙ্কর। রবিশঙ্কর রাজি আছে জেনে, সত্যজিৎ রায় শহরের একটি সাদামাটা স্টুডিও বুক করে ফেলেছিলেন। মাত্র এক রাত সময় কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে যেভাবে পথের পাঁচালীর সুর রবিশঙ্কর করেছিলেন তা এখন ইতিহাস।
মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করেছিলেন পথের পাঁচালীর থিম মিউজিক, যা পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসেবে থেকেসহ ব্যবহার করেছিলেন মাত্র তিনটি বাদ্যযন্ত্র পাখোয়াজ, সেতার আর বাঁশি। আর সেই সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন বেশ কিছু বাংলার গ্রামীণ যন্ত্র যেমন একতারা, দোতারা, সারিন্দা ইত্যাদি। থিম মিউজিকের প্রথমে যখন পাখোয়াজের বাজনা শুরু হয় মনে হয় যেন এক পথ চলার শুরু হচ্ছে ধরা পড়ে জীবনের স্পন্দন বা ছন্দ। আরও গতি আনে সেতার জীবনের মধ্যে গ্রামীণ আভাস আনে বাঁশি। পথের পাঁচালী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, অলোক নাথ ঠাকুর প্রমুখ।
একটি বাঁশের বাঁশিতে তোলা সুর এই চলচ্চিত্রের প্রধান সুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পণ্ডিত রবিশঙ্করের বাদনে দেশ রাগভিত্তিক সুর, রাগভিত্তিক বিষণ্ণ সুরের ব্যবহার করে পথের পাঁচালীর অন্তর আত্মাকে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। এছাড়া সানাইয়ে পটদীপ রাগ সৃষ্টি করে একটি বিশেষ দৃশ্যকে এক নান্দনিক রূপ দান করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও সত্যজিৎ রায় উভয়েই। সর্বজয়া যেখানে হরিহরকে কন্যা দুর্গার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন সেই সময় কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন হরিহর। আর সেখানেই কান্নার শব্দ বাদ দিয়ে রবিশঙ্কর ব্যবহার করেন সানাই-এর তীব্র হাহাকার যার ভাষা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল। বাজিয়েছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর। সেই সুর এতটাই আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে যে নোবেল পাওয়া মার্কিন সাহিত্যিক সল বেলোর ‘হেরজক’ উপন্যাসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে লেখা হয়েছে
Recently I saw Pather Panchali herzog cried with child’s mother win the historical death music started– some musician with a native brass horn imitating shops playing a death noise…’ এরকমই উপলব্ধি ছিল লেখক সলভেলোর। এরপর সত্যজিৎ এর অপরাজিত ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর। সেখানেও টাইটেল সঙ্গীতে যোগ হয়েছিল কিছু দেশীয় বাদ্যযন্ত্র দু মিনিট ২০ সেকেন্ডের এই টাইটেল সঙ্গীতে বেহালা এবং জল তরঙ্গের ব্যবহার মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলেছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল ট্রেনের শব্দ। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চারটে ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর।
সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে রবিশঙ্কর যে সঙ্গীত প্যাটার্নের জন্ম দিয়েছিলেন তা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ভিন্ন ধারার প্রয়োগ করেছিল পথের পাঁচালীর থিম টিউনটিকে। দেবজ্যোতি মিশ্র বলেছিলেন, কল অফ ইনোসেন্স কল অফ পোস্টোরাল পথের পাঁচালী গ্রামীণ জীবন ধরা পড়েছিল এক আন্তর্জাতিক মোহনায় আর সেই মাধ্যম ছিল অনেকটাই সঙ্গীত। পথের পাঁচালীর কম্পোজিশন আন্তর্জাতিক স্তরে সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রে সিগনেচার টিউন হয়ে ওঠে। পথের পাঁচালী এক একটা চলচ্চিত্র যেন এক একটা যুগ, অধ্যায়।